জাগরী-সতীনাথ ভাদুড়ী

যদি জানি যে কাল খুব ভোরে আমার ফাঁসী, তাহলে কি সারারাত্তির জেগে থাকবো আমি? এ প্রশ্ন ভীষণই অবান্তর। ঠিক তেত্রিশ বছর বয়সে এসে যদি আমাকে জেলের এক নম্বর সেলে স্থানান্তর করা হয় তবে পৃথিবীটার দিকে নতুন করে তাকাতে ইচ্ছে হবেই। ফাঁসী কার্যকর করার সুবিধার্থে এই কাজ করা যে জেলের রীতি, তা জানা থাকলে সেলের ছোট্ট জানালা দিয়ে যতটুকু আকাশ দেখা যাবে, ইচ্ছে করবে যতটা পারা যায় তারই দিকে চেয়ে থাকতে। গভীর মায়া হবে গরাদ গলে আসা বিড়ালটার জন্যে। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদির পাতে রোজকার যে অখাদ্য খাবার আসে, তাতে কালেভদ্রে পাওয়া মহার্ঘ দইটুকুও দিয়ে দেয়া যাবে বিড়ালটাকে। কিন্তু জেলের কর্তা সাহেবরা দল বেঁধে এলে তাদের কাছে কোনো শেষ ইচ্ছের কথা বলার লোভটাকে হয়তো সামলাতে পারবো না।
বিলু পেরেছে। তীক্ষ্ণ আত্মসচেতনতায় সে খেয়াল রেখেছে যেন তার কোনো আচরণ থেকেই মনে না হয় যে এই ফাঁসীর রায় তাকে কোনোভাবে দুর্বল করতে পেরেছে। তার সবচে আদরের, সবচে স্নেহের ছোটভাই নীলুই যে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে, ও বিষয়টাকে বার বার ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেও যে বার বার তা মনে পড়েছে, তার জন্য কি নিজেকে ধিক্কার দেয়নি সে? মা, বাবা, জ্যাঠাইমা, সরস্বতী – সব ছাপিয়ে তার কি বার বার নীলুকেই মনে পড়েনি? সুতীব্র অভিমান সত্ত্বেও নীলুকে সে ভালোইবেসেছে। বিলু ভাবতে চেয়েছে যে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সেই সাক্ষ্যটা তার ভাই নয়, দিয়েছে এক দৃঢ়চেতা রাজনৈতিক কর্মী। তাই সে এই কাজ করেছে নিজের দলের স্বার্থে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। আর এইসব টানাপোড়েনের ন্যারেটিভে পাঠক ভালোবেসে ফেলেছে বিলুকে। চোখের আশেপাশে তার বাষ্প ঘন হয়ে এসেছে পাঠকের, যখন বিলু ভাবছে যে তার আত্মত্যাগের স্মরণে তার নামে হয়তো একটা পুরো এলাকারই নতুন করর নামকরণ হবে। আহারে ছেলেটা! এই কি তার চলে যাওয়ার বয়স?

বুক ভারী হতে হতে গল্পের রাত গড়াবে। রাতের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর শব্দের তারতম্য, বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে ব্ল্যাকআউটের প্রচেষ্টা বিনষ্ট করা জোরালো আলোর নিচ থেকে রাতের ডিউটির ‘গিনতি মিলানো’র হাঁক, অন্য সেলগুলোতে কল্পিত কার্যকলাপের সমস্ত বর্ণনা মিলে হু হু করে উঠবে মন, আহা! হতে কি পারে না একটা মিরাকল, গল্পে যেমন হয়েই থাকে, যাতে এই ছেলেটার কাল সকালে কিছুতেই ফাঁসী না হয় কাল? যদি হতেই হয়, অন্তত কাল ভোরেই যেন কিছুতেই না হয়। আর একটু নাহয় থাকুক, ও এই পৃথিবীর হাওয়া দেয়ালে!
তবু স্নায়ুর উত্তেজনা পাঠককে জোর করে টেনে নামাতে হয়। কারণ, এখনো বইয়ের অনেক পাতা বাকি। কারণ, জেলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় গান্ধীবাদী আশ্রমনিবাসী বাবা যে উচ্চ মর্যাদার রাজবন্দীদের সেলে জেগে আছেন, সেখানে গল্পটা বলা হয় ভিন্ন গলায়। এই গলাটা, এই বলাটা বাবার। যিনি ভাবতে থাকেন যে স্কুলের হেডমাস্টারের চাকরিটা ছেড়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বার্থে আশ্রম স্থাপন করে পুরোপুরি জীবন বদলের সিদ্ধান্তটা না নিলে হয়তো বিলুকে আজ ফাঁসীর সেলে থাকতে হতো না। হয়তো নীলুরও এমন মন হতো না যা তার দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার মতো কঠোর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু লোকে যাতে ভেতরের এই যন্ত্রণাগুলোকে কিছুতেই বুঝতে না পারে, সেই গাম্ভীর্যটুকু বজায় রাখার চেষ্টা ছাড়তে পারেন না তিনিও। এদিকে বিলুর সেলে মশারী নেই ভেবে কিছুতেই নিজের বিছানায় মশারী ব্যবহার করবেন না। বিলু কী না কী খাচ্ছে ভেবে মুখে রুচবে না কিছুই। বিরাট হলঘরে প্রথম শ্রেণীর সুবিধাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় কয়েদিরা নিজেদের মধ্যেকার ক্ষুদ্র জেল স্বার্থ ও বৃহত্তর রাজনৈতিক অবস্থানের বিভেদ ভুলে গিয়ে এই চরখা কেটে দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা করা প্রৌঢ়বয়সী পিতাকে ব্যস্ত রাখতে চাইবেন। যাতে ফাঁসীর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আসা গাড়িগুলোর ইঞ্জিনের শব্দ কিছুতেই তার কান পর্যন্ত না পৌঁছায়।
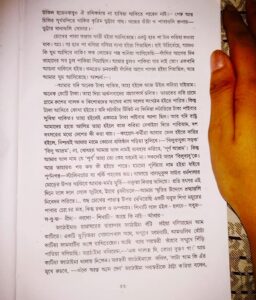
তারপরে আসবে ‘আওরাত কিতা’। নারীদের বন্দীশালা। এখানে এসে মায়ের বচন লেখা হয় চলিত ভাষায়। পাঠক কয়েক পাতা উল্টে-পাল্টে দেখে, আরে, কোনো ভুল হয়নি তো? না। ঠিকই আছে। মা দিব্যি তার নিজের মনের রাগ, ক্ষোভ, উৎকণ্ঠা – সব প্রকাশ করছেন চলিত বাংলায়। এবং এইখানে এসে পাঠক কিঞ্চিৎ চিন্তায় পড়ে যায় যে কেন বাকি দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্ণনাগুলো সাধুভাষায় লেখা হলেও মায়ের কাছে এসে ভিন্নরূপ? তা যাক, লেখক নিশ্চয়ই জীবিত থাকলে সে উত্তর দিতে পারতেন। কিন্তু এখন তো আর সে উপায় নেই। ফলে, মায়ের মনের আকুলি বিকুলি এবং প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একসময় পাঠক মূলত দুইজন দোষীকে চিহ্নিত করতে পারে। প্রথমজন মহাত্মা গান্ধী, যার প্রতিটি বাক্য অনুসরণ করার চেষ্টায় দ্বিতীয়জন, অর্থাৎ তার স্বামী গোটা জীবনটাকেই জটিল করে তুলেছিলেন। স্বামীর মতো তিনিও ভাবেন যে সামাজিক যোগ্যতায় সমান না হলেও যদি সরস্বতীর সাথে বিলুর বিয়েতে রাজি হয়ে যেতেন, তবে হয়তো তার ছেলের এই দশা তাকে দেখতে হতো না। শতবার করে তাই নিজেকেও দুষতে থাকেন তিনি। এবং কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না যে তার ছোট ছেলে, যে কিনা চিরকাল ছিল ভাই অন্তপ্রাণ, সে কী করে তার দাদার মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে। তবু, হয়তো রাজনৈতিক আবহের মধ্যে প্রায় গোটা জীবন কাটিয়ে দেয়ার অভিজ্ঞতার কারণেই তিনি যথেষ্ট শক্ত থাকার চেষ্টা করেন এবং ঈঙ্গিতে পাশের ঘরের যে ফুলপ্রেমী বন্দিনী তাকে রোজ রোজ ফুল দিয়ে যান, তার হাত দিয়ে ফুলগুলো পাঠাতে চান বিলুর জন্য। ছেলেটা ফুল বড্ড ভালোবাসতো কিনা! ততক্ষণে পাঠকও সে ভালোবাসার কথা জেগে গেছে, কারণ বয়ানের শুরুর দিকেই বিলু তার সাথে জাফরান রঙের বেগ্নুনিয়ার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। শিশুগাছের ওপর লতিয়ে ওঠা সেই ফুলগুলোকে আকাশের পটভূমিতে রেখে তিরঙ্গার সে চিত্রকল্প লেখক বিলুর ভাষাতে প্রকাশ করেছিলেন, পাঠকের বিশ্বাস যে বহু বহুদিন সেই ছবি তার মনে স্পষ্ট জেগে থাকবে।
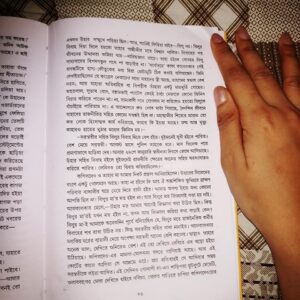
সবশেষ অধ্যায় শুরু হলে পর পাঠক বেশ কয়েকবার ভাববে, যদি আর না এগোই তো বিলু তো বেঁচে থাকলো। কারণ, এখনো তো লেখক স্পষ্ট করে ফাঁসীর বর্ণনা দেননি। আচ্ছা, গাড়ির শব্দ শুনতে পেয়েছে সকলেই, তা মানলেও ফাঁসীটা যে হয়েই গেছে তা তো নাও হতে পারে। কিন্তু এই ভীষণ চতুর ইচ্ছেটাকে মেরে ফেলে আরেকটা উদগ্র কৌতুহল। কেমন ভাই নীলু? একটা ভাই, যে তার বাবার আশ্রমের উপার্জন প্রত্যাখ্যান করে দাদার সম্মানীর টাকাতে কলেজে পড়েছিল, সে সেই দাদারই মৃত্যুপরোয়ানাকে নিশ্চিত করে তোলে কী করে? প্রাণে ধরে এই কাজ কেউ কী করে করতে পারে, তার সেই নিজস্ব ব্যাখ্যা জানতে চাওয়ার লোভটা সংবরণ করতে পারে না বলেই জেলগেটে নীলুর সাথে দেখা হয় পাঠকের। নীলু পরিবারের পক্ষ থেকে তার প্রিয় দাদার লাশ গ্রহণ করতে এসেছে। সে এর আগে দাদাকে বহুবার দেখতে এসেছে। জেলের কর্মচারীদের উপরি টাকা দিয়েছে, যাতে দাদার সেলে ভালো খাবার পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে তারা। এত মায়া নিয়ে তার কি একবারও মনে হয় না যে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়াটা একেবারেই উচিৎ হয়নি? একেবারে শৈশব থেকে দাদার প্রভাব বলয়ে থাকতে থাকতে মাত্রই কয়েক বছর আগে পাওয়া এক ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ কি তার কাছে এতই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল? নাকি আসলে সে যে তার দাদার প্রভাব বলয়ের বাইরে আসতে পারে, এই সত্যটা সবাইকে, অথবা নিজেকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া বেশি জরুরী ছিল? থাক, সে উত্তর পাঠক বরং নিজের স্মৃতিতে তুলে রাখুক।
তারমানে পুরোটা মিলে, ‘জাগরী’ মূলত একটা পুরো রাত জেগে থেকে ভোর করার বয়ান, একই পরিবারের চারজন ব্যক্তির ভিন্ন বর্ণনায়। মূলত প্রতিটাক্ষণ একটা তেত্রিশ বছরের যুবকের ফাঁসী হয়ে যাচ্ছে, এই বেদনাকে মেনে নিতে পারার ফলে অসম্ভব জেনেও একটা মিরাকলের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রাতটা ভোরের দিকে যাত্রা করে। এর মাঝে জেলজীবনের খুঁটিনাটি জানতে পাওয়া যায়, আবহে সবসময় বাতাসের মতো ঝুলে থাকে ইতিহাসের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জেলের ভেতরের ও বাইরের জীবনের বিবরণ আর মানুষের মনের ভেতরে চলতে থাকা নিজস্ব চিন্তাধারার এক অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য পাঠ হয়ে ওঠে এই উপন্যাস। তাই পাঠক যখন জানতে পারে যে এটি ছিল ভাদুড়ী মশাইয়ের প্রথম উপন্যাস, তখন আরেকটা বার মনে হয় যে জীবনে আসলে কিছুই করে ওঠা গেল না।
আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা এ উপন্যাস মনে করাবে ইতিহাসের সেইসব যোদ্ধাদের, যাদের কর্মের ছাপ পৃথিবী মনে রাখুক বা ভুলে যাক, যারা প্রত্যেকেই নিজের চাইতে অথবা ব্যক্তিগত ইতিহাসের চাইতে বড় কিছু হতে চেয়েছিলেন। যাদের কাছে জীবনের চাইতে মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, পরিবারের চাইতে রাজনীতিকে যারা গুরুত্ব দিতেন বেশি। একইসাথে পাঠক মনে মনে ধন্যবাদ দেবে উপন্যাস লেখার সময়টাকেও। কেননা তিনটি ভিন্ন রাজনৈতিক ধারার দ্বন্দ্ব ও তার অনুসারীদের অন্তর্কলহ নিয়ে লেখা হলেও উপন্যাসটি গত শতকের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়ে ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছিল। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কারের প্রথম গ্রহীতাও ছিল এই উপন্যাস। ফলে, সময়কে ধন্যবাদ দিতেই হয়, সেসময়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো কঠোর বেষ্টনী ছিল না বলে। তখনো গল্পকে জীবন থেকে লেখা যেত বলেই হয়তো পাঠক কল্পনা করার সুযোগ পায় যে ‘জাগরী’র বিলুবাবুর ছবিটা আসলে লেখক তার নিজের জেলজীবনের অভিজ্ঞতার রসদ নিয়ে, নিজেরই আদলে তৈরি করেছিলেন।
মার্জিয়া রহমান




সাম্প্রতিক মন্তব্য